ফার্মগেটের ফুটপাথে নিজের তাজা রক্তের মধ্যে নিথর হয়ে পড়ে থাকা মানুষটি সেদিন সকালে কিছু প্রিয়জনের অপেক্ষা উপেক্ষা করেই হয়তো কোনো জরুরি প্রয়োজনে ঘর ছেড়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে, সে আর ফিরবে না। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক নিদারুণ অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল তার জীবন। সে জানতেও পারলো না, কী এমন তার অপরাধ ছিল যে তাকে একদিনের জন্য সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়ে সব শেষ করে দেওয়া হলো। তার এই অকাল মৃত্যুর জন্য দায় আসলে কার? কেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবন এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কাছে এতটা তুচ্ছ?
মেট্রোরেলের বেয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে যখন আবুল কালামের মতো একজন মানুষের প্রাণ গেল, তখন হাস্যকরভাবে শোনা গেল— "বিশেষজ্ঞ"রা নাকি আগেই বিপদ সংকেত দিয়েছিলেন, কিন্তু "কর্তৃপক্ষ" সেই সতর্কবাণীকে পাত্তাই দেয়নি। বাংলাদেশে যেকোনো বড় বিপর্যয়ের পর এই একই কথা বারবার শোনা যায়। আমাদের দেশে ‘কর্তৃপক্ষ’ যেন এক দুর্ভেদ্য, ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা অদৃশ্য শক্তি, যার কোনো জবাবদিহি নেই। এই অদৃশ্য শক্তি মানুষের জীবনের মূল্য দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়।
মেট্রোরেলের দুর্ঘটনায় নিহত আবুল কালামের পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে যে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল, তা জনগণের কাছে এক প্রকার উপহাস বা 'মকারি' হিসেবে প্রতীয়মান। মেট্রোরেলের মতো একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর চরম গাফিলতির কারণে একজন মানুষের তাজা প্রাণ চলে যাওয়ার পর, এই সামান্য পরিমাণ অর্থ সহায়তা আসলে মানুষের জীবনের মূল্যকে তুচ্ছ করে দেখারই নামান্তর। তবে, মেট্রোরেল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পরবর্তীতে নিহতের পরিবারকে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।
সাধারণ জনগণের মধ্যে এই ক্ষোভ জন্ম নেয় যে, একটি জীবন এবং সেই পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতির বিপরীতে (পাঁচ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত ১০ কোটি টাকা) এই অর্থ সহায়তা কেবলই কর্তৃপক্ষের দায় এড়ানোর একটি সস্তা কৌশল। এই ধরনের লোক-দেখানো ক্ষতিপূরণের ঘোষণা জবাবদিহিতার সংস্কৃতিকে আরও দুর্বল করে এবং রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার কাছে সাধারণ মানুষের জীবনের গুরুত্বহীনতাকেই বারবার তুলে ধরে।
মেট্রোরেলের বেয়ারিং প্যাডজনিত ত্রুটির বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিশেষজ্ঞ দল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট সতর্কবার্তা দিয়েছিল, যা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে। বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে এক প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, মেট্রোরেলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে ব্যবহৃত বেয়ারিং প্যাডগুলোর গুণগত মান ও ইনস্টলেশন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বেয়ারিং প্যাডগুলোর ফাটল, ক্ষয় এবং অসম বিন্যাসের (uneven placement) ঝুঁকি তুলে ধরা হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে পরিবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণের সুপারিশ করা হয়। বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই বেয়ারিং প্যাডগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার শতকরা ৯৫ ভাগ ঝুঁকি ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই তথ্য-ভিত্তিক সতর্কতা আমলে নেয়নি, যার ফলস্বরূপ একজন সাধারণ মানুষের প্রাণহানি হলো। এই উদাসীনতা প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও জননিরাপত্তাকে উপেক্ষা করাই যেন এই অদৃশ্য কর্তৃপক্ষের নীতি।
জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এমন উদাসীনতার আরও একটি ভয়ংকর উদাহরণ হলো পলাশীর মোড়ে সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ শুরু হওয়ার সময় থেকেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, পলাশীর মোড় একটি অত্যন্ত ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাফিক জংশন, যেখানে এই ধরনের স্থাপনা নির্মাণ ট্র্যাফিকের স্বাভাবিক প্রবাহে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।
এই গভীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ফায়ার অডিট এবং সেফটি সার্টিফিকেট হালনাগাদ করা প্রয়োজন। একইসাথে, স্বাধীন ও শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রত্যেকটি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা অপরিহার্য। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তবে সেই ব্যর্থতার দায় সমগ্র রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়।
বুয়েটের গবেষণা তথ্য ও মডেলিং বিশ্লেষণ দেখিয়েছিল যে, স্মৃতিস্তম্ভটি রাস্তার মধ্যখানে অবস্থিত হওয়ায় পথচারী ও যানবাহন উভয়ের জন্যই এটি একটি 'ব্ল্যাক স্পট' বা মারাত্মক দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা তৈরি করবে। তারা জোর দিয়ে বলেছিল যে, কর্তৃপক্ষের এমন একটি ত্রুটিপূর্ণ নকশার বাস্তবায়ন আরও অনেক মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু সরকারের অদৃশ্য কর্তৃপক্ষ সেই সতর্কতাকেও বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি, যেন তারা আরেকটি আবুল কালামের মতো মর্মান্তিক মৃত্যুর অপেক্ষা করছে—যা কেবল আরো একটি পরিসংখ্যান হয়েই থাকবে।
জনগণের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই ধরনের অবহেলা কেবল প্রযুক্তিগত বা অবকাঠামোগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি আইন প্রয়োগ এবং তদারকির ক্ষেত্রেও চরম দুর্বলতা প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে (২০২০–২০২৪) দেশে মোট অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ৯৯০টি আগুন ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়েছিল (প্রতিশোধ, শত্রুতা বা সংঘাতের কারণে), যাতে ৭২০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এই তথ্য স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কেবল দুর্ঘটনা নয়, বরং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চরম ব্যর্থতা ও ঢিলেঢালা তদন্তের সংস্কৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধগুলোকেও বাড়তে সাহায্য করেছে। যদি অপরাধীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেত, তবে ইচ্ছাকৃত নাশকতার এই প্রবণতা এতটা বাড়ত না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিহীনতার কারণে সমাজের অপরাধী চক্রগুলো মানুষের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এই ধরনের কাজ করার সাহস পাচ্ছে।
এই ধারাবাহিক বিপর্যয়ের আরেকটি গভীর উদ্বেগের কারণ হলো, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে পেশাদারিত্বের নতিস্বীকার। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ি বা নৌযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া, রাসায়নিক গুদামের লাইসেন্স প্রদান করা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রায়শই রাজনৈতিক চাপ বা মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন কাজ করে। যখন একজন বিশেষজ্ঞ বা সরকারি কর্মকর্তা নিয়ম মেনে কাজ করতে চান, তখন এই অদৃশ্য কর্তৃপক্ষ তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বা তাদের সরিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিই নিশ্চিত করে যে, দেশের আইন-কানুন বা বিজ্ঞানভিত্তিক সতর্কতা কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর বাস্তবে দুর্নীতিপরায়ণ প্রভাবশালী মহল জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ পায়। এই অদৃশ্য কর্তৃপক্ষ আসলে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার এক সম্মিলিত শক্তি, যার প্রধান লক্ষ্য হলো নিজেদের ক্ষমতা এবং পকেট ভারী করা—সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নয়।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জনমনে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে (২০২০–২০২৪) দেশে মোট অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ১ লাখ ২১ হাজারেরও বেশি। শুধু ২০২৪ সালেই সারা দেশে মোট ২৬,৬৫৯টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৪০ জন। এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চরম ব্যর্থতার কারণে মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে পড়ছে।
অক্টোবর ২০২৫-এর মাঝামাঝি সময়ে ঘটে যাওয়া মিরপুরের শিয়ালবাড়ী অগ্নিকাণ্ড একটি মর্মান্তিক উদাহরণ। রূপনগরের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটি পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ আগুনে ১৬ জন নিহত হন। তদন্তে দেখা যায় এই কারখানা বা গুদামটির কোনো বৈধতা ছিল না। একইভাবে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শত শত কোটি টাকার পণ্য পুড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ঘটনাগুলি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতারই ইঙ্গিত দেয়।
এই ধরনের দুর্ঘটনার পেছনের মূল কারণ প্রায় একই— গাড়ির ফিটনেস নেই, চালকের যোগ্যতা নেই, রাসায়নিক গুদাম বা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির বৈধ কাগজপত্র নেই। অথচ "কর্তৃপক্ষ" এসব বিষয়ে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেয় না। আমাদের শহর ও জনপদের অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলোর দৈন্যদশা নিয়েও কর্তৃপক্ষের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। একটি প্রশ্ন বারবার আসে: কেন দুর্ঘটনা ঘটবে জানার পরও কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকে? উত্তর হয়তো একটাই— এই অদৃশ্য শক্তির কাছে সাধারণ মানুষের জীবনের চেয়ে তাদের স্বার্থ ও দুর্নীতিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
সাম্প্রতিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, কারখানা এবং জনবহুল এলাকায় একের পর এক বড় অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা, এই প্রশ্ন এখন রাজনৈতিক আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও ফায়ার সার্ভিসের সাবেক কর্মকর্তারা বলছেন, এই ঘটনাগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করার প্রচেষ্টা হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের সন্দেহের আঙুল উঠেছে বিভিন্ন পক্ষের দিকে। যদিও কোনো দলের সংশ্লিষ্টতার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মেলেনি, তবুও এই ধারাবাহিক বিপর্যয়কে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির কৌশল হিসেবে দেখছেন অনেকে।
জুলাই আন্দোলনের পর অনেক আবেগপ্রবণ মানুষ হয়তো পরিবর্তন আশা করেছিল, কিন্তু দেখা গেলো, এই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা অদৃশ্য "কর্তৃপক্ষ" হাজারগুণে ক্ষমতাবান আর অবিচল এক শক্তি। জনগণের প্রত্যাশা পূরণ তো দূরের কথা, তারা উল্টো আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। প্রতিটি দুর্ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও, দায় এড়ানোর চিরায়ত সংস্কৃতিতে কারণ হিসেবে 'শর্টসার্কিট' বা 'যান্ত্রিক ত্রুটি'কে দায়ী করা হয়। সাধারণ মানুষ মনে করে, এর মাধ্যমে দোষীদের বাঁচিয়ে দেওয়া হয় এবং জবাবদিহির অভাব আরও প্রকট হয়।
এই অব্যবস্থাপনা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেও বাধাগ্রস্ত করছে। শাহজালাল বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেপিআই (Key Point Installation) এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে পারে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে নাশকতামূলক আগুন শনাক্ত করার মতো সক্ষমতা নেই। ফলে বড়-ছোট সব আগুনকেই নিছক 'দুর্ঘটনা' হিসেবে গণ্য করা হয়, যা একটি বড় দুর্বলতা। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কিছু ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে বীমা জালিয়াতির মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।
জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান এই সংশয় এবং আস্থাহীনতা কেবল অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনাস্থাকেই তুলে ধরে। তারা দেখছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ— সব ক্ষেত্রেই অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির অদৃশ্য থাবা। মেট্রোরেলের বেয়ারিং প্যাড খুলে পড়া, কেমিক্যাল গুদামে অগ্নিকাণ্ড বা সড়ক দুর্ঘটনা— সব ঘটনাই এক সূত্রে গাঁথা, যার নাম 'কর্তৃপক্ষের নির্বিকার ঔদাসীন্য'। এই ঔদাসীন্যের মূল উৎস হলো জবাবদিহিতার সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যাওয়া।
এই নৈরাজ্যের আড়ালে একটি গভীরতর সংকট লুকিয়ে আছে, আর তা হলো— রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং সমন্বয়হীনতা। ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন, রাজউক এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা বা অবৈধ গুদামগুলো বছরের পর বছর ধরে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। প্রতিটি সংস্থা তাদের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়।
এই গভীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ফায়ার অডিট এবং সেফটি সার্টিফিকেট হালনাগাদ করা প্রয়োজন। একইসাথে, স্বাধীন ও শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রত্যেকটি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা অপরিহার্য। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তবে সেই ব্যর্থতার দায় সমগ্র রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়।
এই অদৃশ্য 'কর্তৃপক্ষ' তাদের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিবর্তে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রকল্পগুলোতে অর্থ ও মনোযোগ বিনিয়োগের মাধ্যমে জনগণের নিরাপত্তা ইস্যুটিকে আরও বেশি অবহেলা করছে। সরকার মেগা প্রকল্প এবং বিলাসবহুল নির্মাণকাজে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করলেও, দেশের জরুরি সেবাসমূহ যেমন ফায়ার সার্ভিস, হাসপাতাল বা নিরাপদ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে সেই পরিমাণ মনোযোগ বা বিনিয়োগ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। যখন আবুল কালাম মেট্রোরেলের নিম্নমানের বেয়ারিংয়ের শিকার হন, তখন বোঝা যায়, অবকাঠামোর সৌন্দর্য বা রাজনৈতিক প্রচারণামূলক মূল্য (propaganda value) সাধারণ মানুষের নিরাপদ জীবনের সাংবিধানিক অধিকারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই অগ্রাধিকারের ভুল বিন্যাসই প্রমাণ করে যে, জনগণের অর্থে পরিচালিত হলেও রাষ্ট্রের এই অদৃশ্য কাঠামো আসলে জনস্বার্থের বিপরীতেই অবস্থান নিয়েছে।
আমাদের এই অসহায়ত্বের মুখে এখন প্রশ্ন একটাই— কবে এই অদৃশ্য কর্তৃপক্ষকে মানুষের জীবনের মূল্য দিতে এবং তাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হবে?
লেখক : সিইও, ইটিসি ইভেন্টস লিমিটেড।
এইচআর/জেআইএম

 3 days ago
9
3 days ago
9



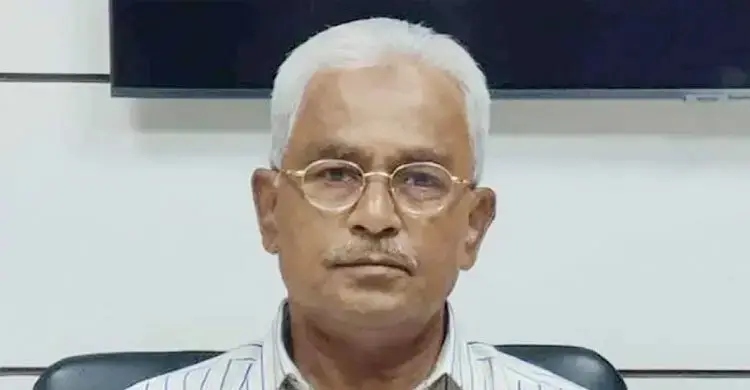





 English (US) ·
English (US) ·