বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক ডিজিটাল রূপান্তর এবং দ্রুত নগরায়ণের এক চমকপ্রদ পর্যায়ে অবস্থান করছে। বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত এই অগ্রগতির চিত্রটি একদিকে যেমন আশার সঞ্চার করে, তেমনি এর নেপথ্যে জমে উঠছে এক নীরব এবং সুদূরপ্রসারী সামাজিক সংকট—তা হলো প্রজন্মগত বৈষম্য। এই প্রজন্মগত বৈষম্যের শিকার হলো দেশের যুব সমাজ, যারা প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ, উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্বজনীন চিন্তাধারায় অভ্যস্ত। কিন্তু তারা ক্রমশ অনুভব করছে যে সমাজের সিঁড়িতে আরোহণ করা তাঁদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন, এমনকি অসম্ভব।
শিক্ষা, কর্মসংস্থান, এবং সম্পত্তি মালিকানার ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত বাধাগুলো দৃঢ়মূল হয়েছে, তা নতুন প্রজন্মকে এক প্রকার অদৃশ্য 'ফাঁদে বন্দি' করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অসঙ্গতি নয়; এটি একটি গভীর সমাজতাত্ত্বিক সঙ্কট, যেখানে পিয়ের বুরদিয়ু ও কার্ল মার্কসের সামাজিক পুনরুৎপাদনের তত্ত্বসমূহ বাস্তবের মাটিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।
সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বুরদিয়ুর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সমাজে বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক পুঁজির মাধ্যমে টিকে থাকে না, বরং এটি সাংস্কৃতিক পুঁজি এবং সামাজিক পুঁজির মাধ্যমেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। এই পুঁজিগুলো পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে সুযোগের ক্ষেত্রকে সীমিত করে দেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদিও দেশের শিক্ষা খাত প্রভূত সম্প্রসারিত হয়েছে, সেই শিক্ষা কিন্তু সকলের জন্য সমান সুযোগের দরজা উন্মুক্ত করতে পারেনি।
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যয়বহুল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যম এবং বিদেশি ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অদৃশ্য শ্রেণি বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাজন বুরদিয়ুর 'সাংস্কৃতিক পুঁজি'র ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে—যেখানে শুধুমাত্র মেধা বা একাডেমিক ফলাফল নয়, বরং 'সঠিক ধরণের শিক্ষা', 'সুবিধাজনক সামাজিক সংযোগ' এবং প্রাতিষ্ঠানিক 'সঠিক অভ্যাস' বা আচরণবিধি নির্ধারণ করে কে সফল হবে এবং কে প্রান্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রান্তিক অঞ্চল বা দুর্বল সামাজিক পটভূমি থেকে আসা শিক্ষার্থীরা তথাকথিত 'উচ্চ সাংস্কৃতিক পুঁজি'-র অভাবের কারণে প্রথম থেকেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে, যা বৈষম্যের সূচনা করে।
এই কাঠামোগত শিক্ষা বৈষম্য সরাসরি কর্মসংস্থান বাজারের উপর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রতিবছর লাখো তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, কিন্তু তাঁদের মেধা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী পর্যাপ্ত এবং মর্যাদাপূর্ণ চাকরির সুযোগ নেই। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এখনো দেশের বৃহৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র, কিন্তু এই খাত অনিরাপদ, অস্থায়ী, শোষণমূলক এবং প্রায়শই নিম্ন মজুরিভিত্তিক। অপরদিকে, দেশের আনুষ্ঠানিক বেসরকারি খাত এখনো পারিবারিক বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে, যা নতুন প্রজন্মের জন্য ন্যায্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগকে সীমিত করে তুলেছে।
সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক, রাজনৈতিক প্রভাব এবং দীর্ঘসূত্রিতা তরুণদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা সৃষ্টি করেছে। ২০২৪ সালে কোটাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে তরুণদের নেতৃত্বে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল, তা কেবল একটি নিয়োগ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না, বরং প্রজন্মগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের এক গভীর সামাজিক ও প্রতীকী অভ্যুত্থান ছিল।
নতুন প্রজন্ম দয়া চায় না, তারা চায় শুধু সুযোগের সমতা এবং মর্যাদার স্বীকৃতি। তারা চায় বিশ্বাস করতে যে সমাজে প্রচেষ্টা বৃথা যায় না, ন্যায়বিচার কেবল বইয়ের শব্দ নয়, বাস্তবতারও অঙ্গ। প্রজন্মগত বৈষম্য দূর করা মানে কেবল অর্থনৈতিক নীতি সংস্কার নয়—এটি সামাজিক ন্যায়বোধ পুনর্গঠনের এক অপরিহার্য আহ্বান। কারণ যখন একটি প্রজন্ম নিজেদের বন্দি মনে করে, তখন পুরো সমাজের গতিই স্থবির হয়ে যায়, আর তাঁদের মুক্তিই হতে পারে বাংলাদেশের প্রকৃত ও টেকসই অগ্রগতির সূচনা।
কার্ল মার্কসের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এক প্রকার বিচ্ছিন্নতা বা এলিয়েনেশন-এর মধ্যে বসবাস করছে। তাঁরা কঠোর শ্রম দিচ্ছেন, পুঁজি বিনিয়োগ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের দক্ষতা বাড়াচ্ছেন—কিন্তু সমাজের মূল কাঠামো তাঁদের এই পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থনীতি যতই প্রসারিত হোক না কেন, শ্রমিক এবং যুব সমাজ ক্রমশ উৎপাদন এবং সম্পদের প্রকৃত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
ডিজিটাল অর্থনীতি, গিগ ইকোনমি বা ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মগুলো প্রথমে 'স্বাধীনতার প্রতীক' বা 'নতুন দিনের সম্ভাবনা' মনে হলেও, বাস্তবে এই খাতগুলো তরুণদের জন্য অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। স্থায়ী চাকরি নেই, নির্ভরযোগ্য মাসিক আয় নেই, অথচ জীবনযাত্রার ব্যয়, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ফলে, তাঁরা 'স্বনির্ভর' হওয়ার চেষ্টা করলেও, প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিকভাবে অরক্ষিত থেকে যাচ্ছেন। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি মানুষের শ্রমের ফল থেকে মানসিক বিচ্ছিন্নতা, যা তাঁদেরকে সমাজের প্রতি আরও বেশি সন্দিহান করে তুলছে।
অর্থনৈতিক পুঁজির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো সম্পত্তি মালিকানা এবং উত্তরাধিকার। পূর্ববর্তী প্রজন্ম, বিশেষত যারা আশির দশক বা নব্বইয়ের দশকে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে জমি বা ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, আজ তাঁরা বিশাল অপ্রাপ্ত আয়ের সম্পদের (unearned wealth) মালিক। এই সম্পদ তাঁদের বর্তমান অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার মূল ভিত্তি। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম, বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্ত তরুণরা, আকাশছোঁয়া সম্পত্তির দামের কারণে ক্রমেই সেই সম্পদ বাজার থেকে ছিটকে পড়ছে।
ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো মহানগরীতে একখণ্ড জমি বা একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করা এখন তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় বা আয়ের নাগালের বাইরে। ফলে, এক প্রজন্মের সঞ্চিত ও সংরক্ষিত সম্পদ আরেক প্রজন্মের জন্য কার্যত ‘অপ্রাপ্য স্বপ্ন’-এ পরিণত হয়েছে। এই অবস্থাকে বুরদিয়ু অর্থনৈতিক পুঁজির প্রজন্মগত সংরক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন—যেখানে ব্যক্তিগত পরিশ্রম বা মেধা নয়, বরং উত্তরাধিকার বা পারিবারিক সংযোগই ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সফলতার মূল নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়।
প্রজন্মগত এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগত নয়, এটি গভীরভাবে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। পুরোনো প্রজন্ম, যারা সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের যুগে বড় হয়েছেন, তাঁরা সামাজিক স্থিতিশীলতা, শ্রেণিবিন্যাস এবং ধৈর্য ধরে সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করার মূল্য বোঝেন। কিন্তু নতুন প্রজন্ম, যারা ইন্টারনেট এবং বিশ্বায়নজনিত তুলনার যুগে বেড়ে উঠেছে, তারা চায় স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতা। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিনিয়ত দেখছে কীভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলিটরা বিলাসী জীবনযাপন করছে, আর তাদের নিজেদের কঠোর পরিশ্রম সমাজে প্রায় অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে। এই ‘তুলনামূলক বঞ্চনা’ (Relative Deprivation) তরুণদের মধ্যে কেবল গভীর হতাশা নয়, বরং সমাজের প্রতি ক্ষোভ, অবিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি সংশয় তৈরি করছে।
সমাজতাত্ত্বিক উলরিখ বেক এবং অ্যান্থনি গিডেনসের “ঝুঁকিপূর্ণ সমাজ” (Risk Society) তত্ত্ব অনুযায়ী, আধুনিক তরুণ প্রজন্ম এমন এক বিশ্বে বাস করছে যেখানে স্থায়ী চাকরি, নিরাপদ পরিবার বা সম্পদের নিশ্চয়তা নেই; বরং প্রত্যেককেই নিজের ভবিষ্যতের দায়ভার নিজেকেই নিতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রকাশ আরও তীব্র। অনেক তরুণ উচ্চশিক্ষিত এবং দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের চরম অনিশ্চয়তার কারণে গভীর মানসিক চাপ, হতাশা এবং সামাজিক একাকিত্বের শিকার হচ্ছে। স্থিতিশীল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা না থাকায় তাঁরা বিবাহ বিলম্বিত করছেন, পরিবার গঠনে অনীহা দেখাচ্ছেন, যা সমাজে জন্মহার এবং সামাজিক বন্ধনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই মনস্তাত্ত্বিক চাপ তাঁদেরকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামাজিকভাবেও দুর্বল করে দিচ্ছে।
২০২৪ সালের তরুণদের নেতৃত্বে সংগঠিত ছাত্র-জনতার আন্দোলন ছিল এই প্রজন্মগত সংকটের একটি প্রতীকী বিস্ফোরণ। এই আন্দোলন কেবল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবি ছিল না, বরং এটি ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন—যেখানে মেধা, কঠোর পরিশ্রম ও সততার মূল্যায়ন হবে পারিবারিক পরিচয় বা সংযোগের ভিত্তিতে নয়। তরুণ প্রজন্মের এই ডিজিটাল যুগের সংগঠনশক্তি সমাজে এক নতুন সামাজিক পুঁজি তৈরি করছে—যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার অভাবকে প্রতিস্থাপন করছে সমবয়সীদের মধ্যে সংযোগ ও সম্মিলিত চেতনা। তাঁরা হয়তো সম্পত্তির মালিক নন, কিন্তু তাঁদের রয়েছে এক অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী ক্ষমতা—যোগাযোগ, জনমত গঠন এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা।
এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি এই বিশাল ও গতিশীল শক্তিকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে পারবে? সমাজতত্ত্বের ভাষায়, বৈষম্যের পুনরুৎপাদন রোধ করতে হলে কেবল নীতিমালায় পরিবর্তন আনাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন একটি গভীর সাংস্কৃতিক রূপান্তর। শিক্ষায় সমতা আনতে গ্রামীণ ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, টেকনিক্যাল ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা, ভূমি ও সম্পত্তি বাজারে যুগোপযোগী সংস্কার আনা, এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও স্বচ্ছ করা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি। কিন্তু নীতির পাশাপাশি প্রয়োজন মানসিক রূপান্তর—একটি নতুন সামাজিক চুক্তি, যেখানে সবাই বিশ্বাস করবে যে পরিশ্রমই সাফল্যের মাপকাঠি, জন্মগত সুবিধা বা বংশ পরিচয় নয়।
প্রজন্মগত বৈষম্য কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয়; এটি বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সামাজিক প্রভাব আরও গভীর, কারণ এখানে তরুণরাই জনসংখ্যার প্রধান শক্তি। যদি এই বিপুল সংখ্যক তরুণ নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হয় এবং সমাজে নিজেদের বন্দি মনে করে, তাহলে সামগ্রিক সামাজিক স্থিতি নষ্ট হবে। ইমিল ডুরকহেইমের ভাষায়, এই অবস্থাকে বলা যায় অ্যানোমি (Anomie)—এক প্রকার নৈতিক ও সামাজিক বিভ্রান্তি, যেখানে মানুষ জানে না কোন নিয়ম অনুসরণ করবে বা কী বিশ্বাস করবে। এমন পরিস্থিতি হয় সমাজকে ভেঙে দেয়, নতুবা তাকে একটি নতুন পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে।
সুতরাং আজকের প্রশ্ন শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয়, এটি একটি গভীর নৈতিক প্রশ্ন—আমরা কি এমন একটি সমাজ গড়ে তুলছি, যেখানে নতুন প্রজন্ম নিজেদের সম্ভাবনাকে স্বাধীনভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে, নাকি আমরা এমন এক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখছি, যেখানে অতীতের সুবিধাভোগীরাই ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করে চলেছে? বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের উপর। যদি রাষ্ট্র এবং সমাজ এই তরুণদের প্রতিভা, ক্ষোভ এবং ন্যায্যতার দাবিকে অনুধাবন করে, তবে এটি হতে পারে একটি নতুন সামাজিক চুক্তির সূচনা—যেখানে সুযোগ হবে ন্যায্য, শ্রম হবে মূল্যবান, এবং অগ্রগতি হবে সকলের জন্য যৌথ। কিন্তু যদি এই গভীর আহ্বান উপেক্ষিত হয়, তাহলে প্রজন্মগত হতাশা একদিন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিস্ফোরণে রূপ নিতে বাধ্য।
নতুন প্রজন্ম দয়া চায় না, তারা চায় শুধু সুযোগের সমতা এবং মর্যাদার স্বীকৃতি। তারা চায় বিশ্বাস করতে যে সমাজে প্রচেষ্টা বৃথা যায় না, ন্যায়বিচার কেবল বইয়ের শব্দ নয়, বাস্তবতারও অঙ্গ। প্রজন্মগত বৈষম্য দূর করা মানে কেবল অর্থনৈতিক নীতি সংস্কার নয়—এটি সামাজিক ন্যায়বোধ পুনর্গঠনের এক অপরিহার্য আহ্বান। কারণ যখন একটি প্রজন্ম নিজেদের বন্দি মনে করে, তখন পুরো সমাজের গতিই স্থবির হয়ে যায়, আর তাঁদের মুক্তিই হতে পারে বাংলাদেশের প্রকৃত ও টেকসই অগ্রগতির সূচনা।
লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী।
এইচআর/জেআইএম

 2 days ago
10
2 days ago
10







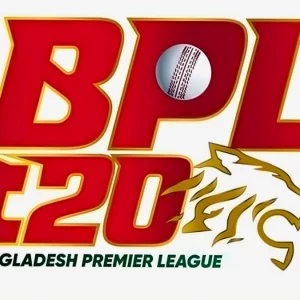

 English (US) ·
English (US) ·